
সমস্যা জর্জরিত স্বাস্থ্য খাত, দুর্নীতি-অব্যবস্থার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান কাম্য
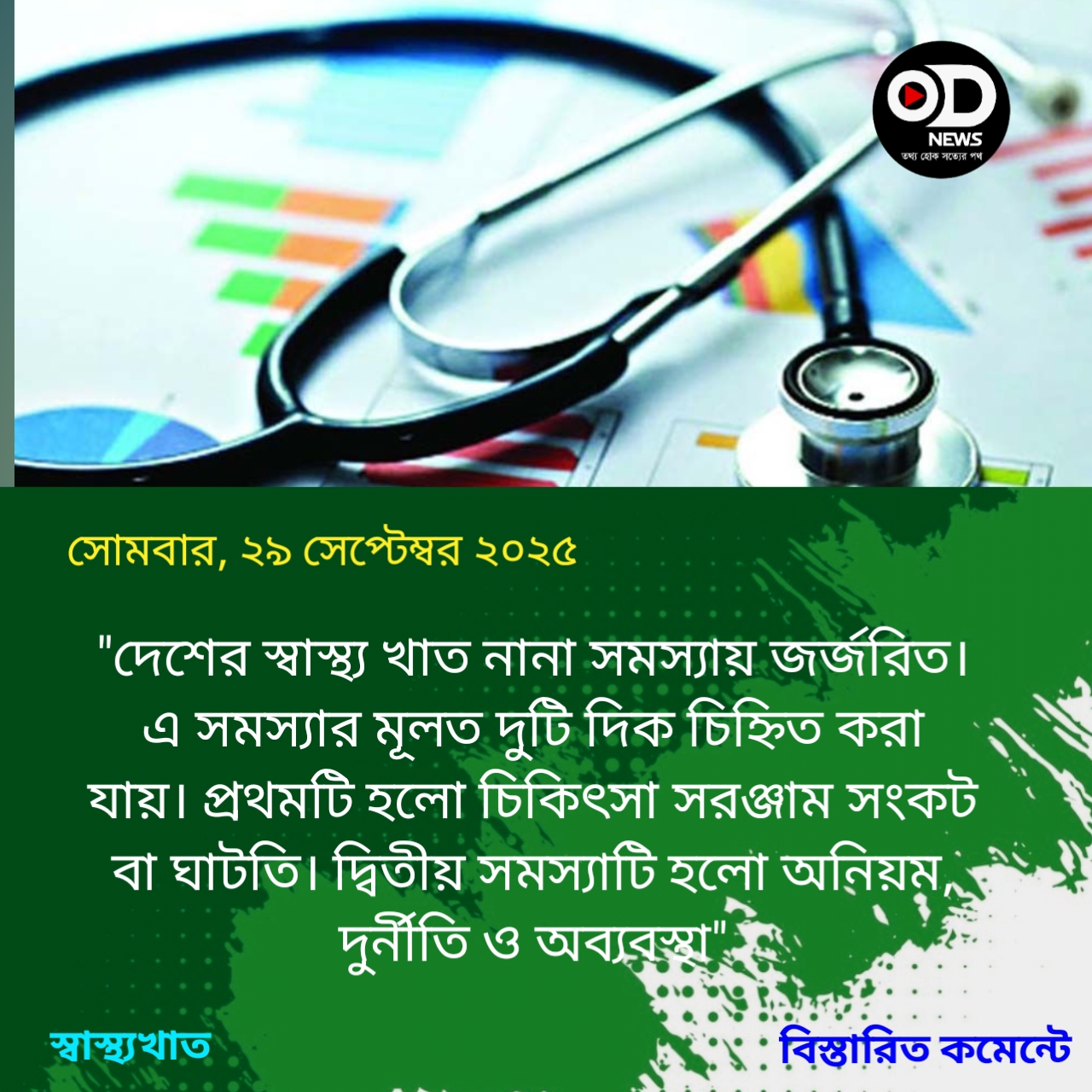
দেশের স্বাস্থ্য খাত নানা সমস্যায় জর্জরিত। এ সমস্যার মূলত দুটি দিক চিহ্নিত করা যায়। প্রথমটি হলো চিকিৎসা সরঞ্জাম সংকট বা ঘাটতি। হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসক সংকট, ফার্মাসিস্ট সংকট, বেড সংকট, ওষুধ সংকট, চিকিৎসা সরঞ্জাম সংকট-এগুলো গণমাধ্যমের নিত্যদিনের খবর। দ্বিতীয় সমস্যাটি হলো অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থা। মেডিকেল কলেজে ভর্তি জালিয়াতি থেকে শুরু করে ডাক্তার-নার্স-টেকনিশিয়ানের বদলি-পদায়ন-স্বাস্থ্য খাতের এমন কোনো দিক নেই যা দুর্নীতিতে জর্জরিত নয়।
কেনাকাটায় চিকিৎসা সরঞ্জামের দাম কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেখানো, প্রশিক্ষিত অপারেটর না থাকার পরও দামি যন্ত্রপাতি কিনে ফেলে রেখে মেয়াদোত্তীর্ণ করে ফেলা-কোনো কিছুই বাদ পড়ে না দুর্নীতির করাল থাবা থেকে।
বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবস উপলক্ষ্যে যুগান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে ৭০০ সরকারি হাসপাতাল থাকলেও সেখানে গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্টদের জন্য কোনো পদ নেই। হাসপাতালে মূলত ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্টরা কাজ করছেন। অথচ ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে শুরু করে দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে থাকেন গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্টরা। রোগীদের নিরাপদ ওষুধ গ্রহণের বিষয়টিও নিশ্চিত করে থাকেন এই ফার্মাসিস্টরা।
এতে বলা হয়েছে, যেসব পরিবার চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোতে স্বাস্থ্যসেবা নিতে গেছে, তাদের মধ্যে ৪৮ দশমিক ৭ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় এ হার ছিল ৪৫ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৫১ শতাংশ। সেবাগ্রহীতা পরিবারের মধ্যে প্রায় ৬ দশমিক ২ শতাংশকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সময় ঘুস দিতে হয়েছে। শ্বেতপত্রে আরও উল্লেখ করা হয়, স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত পণ্যগুলো দরপত্রের মাধ্যমে কেনা হলেও টেন্ডারের প্রক্রিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। হাসপাতালগুলোতে অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা সামগ্রীর সরবরাহে সবসময়ই ঘাটতি থাকছে। কখনো কখনো এই নিয়মিত ঘাটতি পরিস্থিতিকে দুর্নীতির দিকে নিয়ে যায়। বস্তুত স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলো দুর্নীতি ও জবাবদিহিতার অভাবের কারণে সমস্যায় পড়ছে। প্রকিউরমেন্ট সিস্টেমে বড় আকারের আর্থিক অপব্যবহার ও অদক্ষতার অভিযোগও রয়েছে।
স্বাস্থ্য পরিষেবা খাতে একটি সাধারণ প্রবণতা হলো, ওষুধ কোম্পানিগুলো মেডিকেল প্রতিনিধিদের মাধ্যমে চিকিৎসকদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখে, যাতে তারা ওষুধগুলো বাণিজ্যিক নামে (জেনেরিক নামে নয়) লিখে দেন। ফলে ব্যক্তির মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের প্রায় ৭৭ শতাংশই যায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বেসরকারি স্বাস্থ্য খাত একচেটিয়া মুনাফা অর্জন করছে। বেসরকারি হাসপাতালের মাধ্যমে ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো কোনো গুণগত মান ছাড়াই শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাদের কোনো জবাবদিহিতা নেই। আমরা মনে করি, অনিয়ম-দুর্নীতি ও অব্যবস্থা রোধ করা গেলে বিদ্যমান বাজেট দিয়েও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন সম্ভব। কাজেই দুর্নীতি-অব্যবস্থার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়ানো দরকার জরুরি ভিত্তিতে।